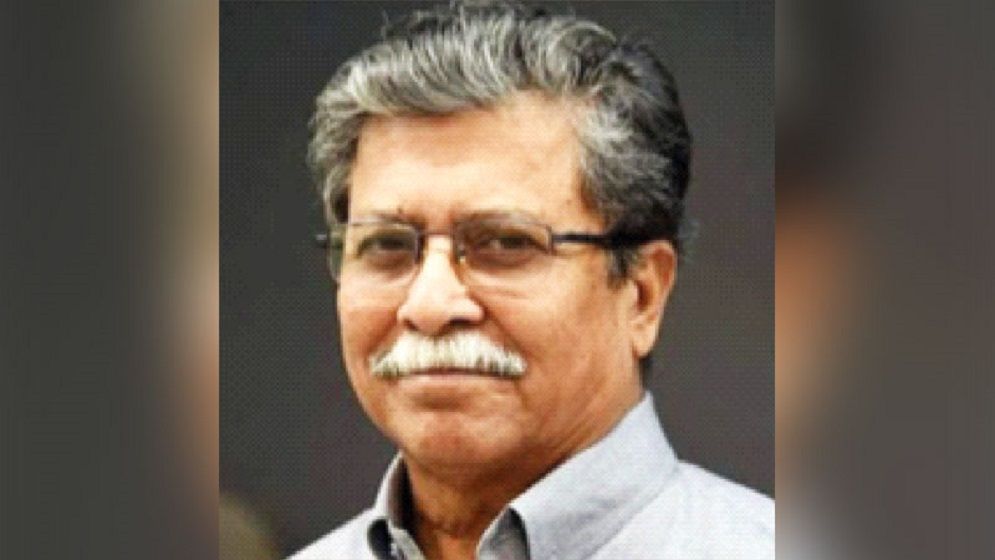
আবু সাঈদ খান
ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জমানায় আলোচিত অনুষ্ঠান ছিল সংবাদ সম্মেলন। না, সংবাদ সম্মেলন বলা যাবে না। সংবাদ সম্মেলনের নামে প্রধানমন্ত্রীর অনুগ্রহভাজন, পত্রিকার সম্পাদক, মালিক, টেলিভিশনের এমডি, সিইও, সাংবাদিক নেতাসহ মিডিয়া হোমরাচোমরাদের আসর বসত। অবশ্য শেখ হাসিনার অতি আদরের দু-চারজন পুঁচকে সাংবাদিকও আমন্ত্রিত হতেন।
বিদেশ সফরে শেখ হাসিনা ছিলেন চ্যাম্পিয়ন। যেখানে সচিব গেলে চলত। সেখানে তিনিই হাজির হতেন। সাধারণত প্রধানমন্ত্রীর বিদেশ সফর শেষে ফিরে আসার দু-এক দিন পর ‘সংবাদ সম্মেলন’ হতো।
প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাংবাদিকদের এড়িয়ে চলেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন না। কারণ, সেখানকার সাংবাদিকরা বড্ড বেয়াড়া! তারা ‘উল্টাপাল্টা’ প্রশ্ন করে নাস্তানাবুদ করে ফেলতে পারেন। মোদি তাঁর দেশের সব সাংবাদিককে বশ করতে পারেননি। যেটি শেখ হাসিনা অনেকাংশে পেরেছিলেন। তিনি মিডিয়া মালিক-সম্পাদক-সাংবাদিকের একাংশকে হাতের মুঠোয় পুরেছিলেন। এসব অনুগত সাংবাদিকই পেতেন প্রধানমন্ত্রীর সংবাদ সম্মেলন বা রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে প্রবেশাধিকার। বেয়াড়া সাংবাদিকদের সেখানে ঢোকার ছাড়পত্র ছিল না।
সংবাদ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখে বিদেশ সফরের ‘সাফল্যগাথা’ বয়ান করতেন। তারপর শুরু হতো প্রধানমন্ত্রীর গুণকীর্তন। তাঁকে বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা, গণতন্ত্রের মানসকন্যা, জাতির ত্রাতা, উন্নয়নের রোল মডেল নির্মাতা, বঙ্গরত্ন, বিশ্বনেতা, হবু নোবেল লরিয়েট ইত্যাদিতে ভূষিত করা হতো। তাঁর মেধা, কর্মক্ষমতা, স্মার্টনেস, শাড়ির রং ও সাজগোজ নিয়ে প্রশংসা চলত। সেই সঙ্গে চলত খালেদা জিয়াসহ বিরোধী দলের নেতাদের, এমনকি বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে ঠাট্টা-মশকরা, উপহাস। এসব সংবাদ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠত একজন দাম্ভিক, নিষ্ঠুর, অতিমাত্রায় কর্তৃত্ববাদী ও স্বৈরশাসকের অবয়ব।
গত ১৬ বছর বেতার-টেলিভিশন-পত্রপত্রিকায় শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের স্তুতি হতো। মন্ত্রী-নেতা-আমলা সমস্বরে শেখ পরিবারের বন্দনা করতেন। পঞ্চদশ সংশোধনীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জাতির পিতা করা হয়। শেখ মুজিবের নামের আগে ‘জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু’ না বললে খেসারত দিতে হতো। বেগম মুজিবের নামের আগে ‘বঙ্গমাতা’ বলতে হতো। শেখ মুজিবের নামে ৯টি বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়েছিল; শেখ হাসিনা, শেখ কামাল ও রাসেলের নামে ক্যান্টনমেন্টের নামকরণ করা হয়েছিল। শেখ পরিবারের নামে দেশজুড়ে ছিল অসংখ্য প্রতিষ্ঠান। অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, বিমানবন্দরে মুজিব কর্নার করা হয়েছিল, স্কুল-কলেজে রাসেল ল্যাব করা হয়েছিল। শেখ মুজিবের অসংখ্য ভাস্কর্য-ম্যুরাল করা হয়েছিল, মুজিব-হাসিনা-কামাল-রাসেলের ছবিতে দেশ ছেয়ে গিয়েছিল। বিমানবন্দরসহ গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লেখা হয়েছিল, মুজিবের দেশ।
এটি ধ্রুবসত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মুক্তিসংগ্রামের প্রধান নেতা। ১৯৬৬ থেকে ১৯৭১ সাল তিনিই মুক্তিসংগ্রামের মুখপাত্র। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ তাঁর পরিবারের সদস্যদের হত্যা করা হয়। তারপর থেকে তিনিসহ মুক্তিসংগ্রামীদের নাম কোনো রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠান বা বেতার-টেলিভিশনে উচ্চারিত হতো না। পাঠ্যপুস্তকেও ছিল না। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর শেখ মুজিবুর রহমান আর উপেক্ষিত থাকলেন না। তিনি স্বমহিমায় আবির্ভূত হলেন। নতুন প্রজন্ম বেতার টেলিভিশনে প্রথম ৭ মার্চে ঐতিহাসিক ভাষণ শুনে উদ্বেলিত হলো। তবে শেখ মুজিবকে বড় করতে গিয়ে ইতিহাসের অন্য নায়কদের ছোট করা হলো।
একাত্তরে শেখ মুজিব ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। তাঁর অবর্তমানে তাজউদ্দীন আহমদই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। শেখ হাসিনার জমানায় তাজউদ্দীন ও মুজিবনগর সরকারের নায়করা ছিলেন ব্রাত্য। শেরেবাংলা আবুল কাশেম ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, মণি সিংহ প্রমুখের অবদান কখনও উল্লেখ করা হতো না। শেখ হাসিনাসহ তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা জিয়াউর রহমানকে পাকিস্তানের এজেন্ট, সিরাজুল আলম খানকে ষড়যন্ত্রকারী বলতেও দ্বিধা করতেন না।
ইতিহাসের নতুন বয়ান তৈরি করা হয়। বেতার-টেলিভিশন ও সংবাদপত্রে অনুগত সাংবাদিক-শিক্ষক-সাহিত্যিকের কণ্ঠে প্রচার করা হতো যে, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আহ্বানে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ৯ মাস যুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এলো। বলা হতো না যে, এই সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে শুরু হলো, কারা নেতৃত্ব দিলেন, রণাঙ্গনে কারা ছিলেন। ঘুণাক্ষরেও উচ্চারিত হতো না যে, কীভাবে জাতীয় পতাকা তৈরি হয়েছিল, কে বা কারা জাতীয় সংগীত নির্ধারণ করেছিলেন। কারা, কখন জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছিলেন। সবকিছুই চাপা পড়ল। শেখ হাসিনার জমানায় বেগম মুজিব, শেখ কামাল, রাসেল প্রমুখের জন্মদিনও জাতীয়ভাবে পালিত হতো। অথচ ১৭ এপ্রিল মুজিবনগর দিবস ছিল উপেক্ষিত।
প্রসঙ্গত, জর্জ ওয়াশিংটন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতার প্রধান নেতা। তবে তিনি এককভাবে জাতির পিতা হিসেবে স্বীকৃত নন। তিনি ও তাঁর অন্য ছয় সহযোদ্ধা (টমাস জেফারসন, জন অ্যাডামস, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, আলেকজান্ডার হ্যামিল্টন, জন জে ও জেমস মেডিসন) যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান ফাউন্ডিং ফাদার। এর বাইরে সংগ্রামে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছেন, এমন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের ফাউন্ডিং ফাদার হিসেবে সম্মানিত করা হয়। এ উপমা তুলে ধরায় অনেকে শেখ হাসিনার আক্রমণের নিশানায় পরিণত হয়েছিলেন।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, শেখ হাসিনার সরকার কী করে ১৬ বছর ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারল? কী ছিল এর রহস্য? ১৯৯৬ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। তখন আওয়ামী লীগ ছিল অনেকটা সংযত। জনমতের বিষয়টি তাদের বিবেচনায় ছিল। ২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে আওয়ামী লীগ বদলে যায়। ক্ষমতা ধরে রাখতে অর্থ ও মাস্তানির পথ অবলম্বন করে। ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ হয়ে উঠল শেখ হাসিনার লাঠিয়াল। লাঠিয়াল বাহিনীতে পরিণত হলো পুলিশও। প্রশাসন, আদালত, বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান সর্বত্রই বসানো হলো শেখ হাসিনার নিজের লোক। দলীয়করণের এক উলঙ্গ চিত্র।
পরিকল্পিত লুটপাটও ছিল সরকারের লক্ষ্য। এ ক্ষেত্রে সোহেল তাজের মন্তব্য প্রাসঙ্গিক। সেটি হলো– ২০০৯ সালে ক্ষমতায় আসার পর শেখ হাসিনা বলেন যে, বিএনপি টাকা বানিয়েছে, আমাদেরও অনেক টাকা বানাতে হবে। এ কথার পর সোহেল তাজ শেখ হাসিনার প্রতি শ্রদ্ধা হারান।
২০০৯ সালে ক্ষমতায় এসে কর্মীদের অর্থ কামাইয়ের সুবিধা করিয়ে দিতে গুরুত্ব দেওয়া হলো অবকাঠামো উন্নয়নের ওপর। গড়ে উঠল অনেক প্রয়োজনীয়-অপ্রয়োজনীয় সড়ক, ভবনসহ নানা স্থাপনা। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ব্যাংকগুলো শেখ হাসিনার অনুগত কতিপয় পরিবারের কাছে তুলে দেওয়া হলো। নিয়মবহির্ভূত ঋণ নিয়ে ব্যাংকগুলো ফোকলা করে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার করা হলো। এই লুটপাটের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও তাঁর পরিবারের যে যোগসূত্র ছিল, তা আজ আর গোপন নেই। মেগা প্রজেক্টে মেগা চুরির মাধ্যমে নেতাদের একাংশ ফুলেফেঁপে উঠল। বলা বাহুল্য, বিএনপির আমলেও দুর্নীতি ছিল। তবে শেখ হাসিনার আমলের তুলনায় তা নস্যি।
এমনই দখলবাজি, চাঁদাবাজির মধ্য দিয়ে যে ধনিক গোষ্ঠী জন্ম নিল; তাদের অনেকেই দেশে টাকা রাখল না, হাজার হাজার কোটি টাকা বিদেশে পাচার হয়ে গেল। ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্যের নেতৃত্বাধীন শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির হিসাবে শেখ হাসিনার শাসনের ১৫ বছরে বিদেশে পাচার হয়েছে ২৮ লাখ কোটি টাকা; যা বাংলাদেশের প্রায় পাঁচটি বাজেটের সমান। এ টাকায় মন্ত্রী-এমপি-আমলা মালয়েশিয়ায় সেকেন্ড হোম, কানাডায় বেগমপাড়া, সিঙ্গাপুর-দুবাই-লন্ডন-সিডনি-নিউইয়র্কের অভিজাত এলাকায় প্রাসাদোপম বাড়ি কিনেছেন, বিদেশে রাজকীয় জীবনযাপন করছেন। আলজাজিরার হিসাব মতে, সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, আরব আমিরাতসহ নানা শহরে ৬২০টি বাড়ি রয়েছে; যার বাজারমূল্য প্রায় ৪৮ কোটি ডলার অর্থাৎ ৫ হাজার ৪৬০ কোটি টাকা। অন্যদিকে ১৬ বছরের নির্মম শাসন-শোষণে নিম্নমধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, বিত্তহীনদের জীবনে সীমাহীন দুর্ভোগ নেমে আসে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, চাঁদাবাজি, দখলবাজি ইত্যাদিতে জনজীবন হয়ে ওঠে অতিষ্ঠ।
শেখ হাসিনার শাসনামলজুড়ে রয়েছে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, গুম ও আয়নাঘরে নির্যাতনের বহু বর্বরোচিত কাহিনি। অসংখ্য রাজনৈতিক নেতাকর্মী-সাংবাদিক-মানবাধিকার কর্মী জেল-জুলুম-নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। বিরোধী দলের সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। কয়েক লাখ বিএনপির নেতাকর্মী ও সমর্থকদের বিরুদ্ধে মামলা তাদের স্বাভাবিক জীবন বিপন্ন করে তুলেছিল। কোনো কোনো নেতার বিরুদ্ধে কয়েকশ করে মামলা ছিল। প্রায় প্রতিদিনই একাধিক মামলায় হাজিরা দিতে হতো। আদালতপাড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের ঠিকানা।
বাক-ব্যক্তি-সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর ছিল সাইবার সিকিউরিটি অ্যাক্টসহ নানা কালাকানুনের খড়্গ। প্রসঙ্গক্রমে, ২০২০ সালে এক অভিযোগে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে লেখক মোশতাক ও কার্টুনিস্ট কিশোরকে জেলে পুরা হলো। বারবার তাদের জামিন প্রত্যাখ্যাত হলো। রিমান্ড-নির্যাতনে ক্ষতবিক্ষত মোশতাকের জীবনপ্রদীপ নিভে গেল। এর এক সপ্তাহ পর কিশোর মুক্তি পান, কিন্তু অমানুষিক নির্যাতনের ক্ষত এখনও বয়ে বেড়াচ্ছেন। একজন কিশোরই নয়; কাজল, খাদিজাসহ অনেকেই সাইবার নিরাপত্তা আইনের নির্মম শিকার হয়েছেন। ভিন্ন মতপ্রকাশের স্বাধীনতায় আগেও বাধা ছিল, তবে শেখ হাসিনার ১৬ বছর এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ।
নিরপেক্ষ নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া হয় পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিধান বাতিল করার মধ্য দিয়ে। ২০১৪ সালে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন হলো। সংগত কারণেই বিএনপিসহ সব বিরোধী দল নির্বাচন বর্জন করল। নির্বাচনে ১৫৩ জনকে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত করা হলো। ২০১৮ সালে ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে বিএনপিসহ বিভিন্ন দল নিয়ে গঠিত জাতীয় ঐক্য ফ্রন্ট নির্বাচনে অংশ নিল। তবে ভোটের আগের রাতে নৌকায় সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা হলো। ২০২৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগী ছাড়া আর কোনো দল ছিল না। এ নির্বাচনকে সবাই উপহাস করে বলত– আমি আর ডামির নির্বাচন। পরপর তিনটি নির্বাচন প্রহসনে পরিণত হলো। এভাবেই কায়েম হলো পরিবারতন্ত্র ও গোষ্ঠীতন্ত্র।
বাকশালও ছিল একনায়কি শাসন, পরিবার ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক শাসন। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ফিরলেন, তখন তাঁর আকাশচুম্বী জনপ্রিয়তা। তিন বছরের মাথায় অনিয়ম, অব্যবস্থা, অদক্ষতা, খুন, দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন, লুটপাটে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে তা তলানিতে নেমে এল। তিনি দেখলেন পায়ের তলায় মাটি নেই। তাই ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে ‘বৈষম্যহীন সমাজের দোহাই পেড়ে চাপিয়ে দেওয়া হলো অগণতান্ত্রিক বাকশালী শাসন। শেখ হাসিনা সেই শাসন ফিরিয়ে আনলেন ভিন্ন কৌশলে, ভিন্ন অবয়বে। শেখ মুজিবের ঘোষিত বাকশালের চেয়ে শেখ হাসিনার অঘোষিত ‘বাকশাল’ ভয়ংকর।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মর্মকথা ছিল অযৌক্তিক কোটা নয়, মেধার ভিত্তিতে চাকরি পাওয়ার অধিকার। সেই আন্দোলন আর সেখানে থাকেনি। ক্ষোভ ও যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসী, শ্রমিক, রিকশাওয়ালা, ফেরিওয়ালা, দোকানি, কেরানিসহ নানা পেশা ও শ্রেণির মানুষ বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থীদের মিছিলে যোগ দিল। বিএনপি, বাম ও ইসলামী দলের কর্মীরাও মিছিলে একাকার হলো। জনগণের ক্ষোভ বাড়িয়ে দিয়েছিল ভোট দিতে না পারার যন্ত্রণা, সেবা খাতের অব্যবস্থা ও পীড়ন এবং পুলিশ ও ছাত্রলীগ-যুবলীগ-স্বেচ্ছাসেবক লীগের নির্যাতন। দিনে দিনে জমে ওঠা পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকে গণবিস্ফোরণ, জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পথিকৃত বিএনপি, গণতন্ত্র মঞ্চ, বাম গণতান্ত্রিক জোট, ফ্যাসিবাদ-বিরোধী বাম মঞ্চ, জামায়াতে ইসলামী, হেফাজতে ইসলামসহ বেশির ভাগ দল আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। অংশ নিয়েছিল লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-বৃদ্ধিজীবীদের একটি ক্ষুদ্র অংশ। তবে ছাত্র-জনতাই অভ্যুত্থানের মূল শক্তি। এটিকে বলা যায়, স্বতঃস্ফূর্ত গণজাগরণ।
অভ্যুত্থানকে অনেকেই বিপ্লব বলছেন। তবে চূড়ান্ত বিচারে এটি বিপ্লব নয়। বিপ্লব আর্থসামাজিক ব্যবস্থা বদলে দেয়; যেমনটি দিয়েছিল রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লব। ফরাসি বিপ্লবও নতুন রাজনৈতিক দর্শনের ঝান্ডা তুলে ধরেছিল।
এটিকে দ্বিতীয় স্বাধীনতা বলার যুক্তি নেই। স্বাধীনতা একবারই এসেছে লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে; যা আমাদের দিয়েছে মানচিত্র, জাতীয় পতাকা, জাতীয় সংগীত ও সংবিধান। এসব সমুন্নত রেখেই পথ চলতে হবে। তবে সংবিধানে যে কালাকানুনের কালো ছায়া পড়েছে তা মুছে ফেলতে হবে।
জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থান নিঃসন্দেহে অনন্য ঘটনা। এভাবে বন্দুকের সামনে সহস্রাধিক নরনারী আত্মদানের ঘটনা ইতিহাসে বিরল। এ অভ্যুত্থান নবজাগরণ এনেছে। জাতীয় ঐক্যের বাতাবরণ তৈরি করেছে। বাঙালি আদিবাসী, প্যান্ট-শার্ট পরা বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজ পড়ুয়া ও টুপি-লম্বা কোর্তা পরা মাদ্রাসা পড়ুয়াদের এক মিছিলে দাঁড় করিয়েছে। আন্দোলনের মিছিলে নারীর উপস্থিতি ছিল ব্যাপক; যা অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ ও রাষ্ট্রের অপরিহার্য উপাদান। আমাদের সমাজে মানুষে মানুষে, ধর্মে বর্ণে যে দূরত্ব তৈরি ছিল, তা ঘুচিয়ে দিয়েছে অভ্যুত্থান।
অভ্যুত্থানের ফসল ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার। জনআকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের দায়িত্ব বর্তেছে তাদের ওপর। সরকারকে খতিয়ে দেখতে হবে, অভ্যুত্থানে অংশগ্রহণকারী ছাত্র-জনতা কী চেয়েছিল, এখনই-বা কী চাইছে? ছাত্র-জনতার মোটাদাগে চাওয়া– বৈষম্যের অবসান, শান্তি, স্বস্তি, ‘আমার ভোট আমি দেব’ অধিকার।
আশার কথা, তিন মাসে অর্থনীতিতে খানিকটা গতি ফিরেছে। ব্যাংকের ওপর জনগণ আস্থা হারিয়েছিল, তা কিছুটা কেটেছে। রেমিট্যান্স প্রবাহ বেড়েছে। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের বাজার নিয়ন্ত্রণে নেই। সিন্ডিকেট এখনও সক্রিয়। অস্থিরতা থামছে না। পরিস্থিতি উত্তপ্ত করে তুলেছে ‘মব জাস্টিস’। ছাত্রদের মধ্যে বিভাজন। ঘটছে নানা অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা।
পুলিশ-প্রশাসন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না। এখনও পুলিশ সক্রিয় নয়। প্রশাসন ঢিমেতালে। জনমনে প্রশ্ন, অন্তর্বর্তী সরকার পারবে তো পরিস্থিতি সামাল দিতে, জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে? ১৬ বছরের জঞ্জাল সরাতে, কাঙ্ক্ষিত সংস্কার আনতে?
এ সরকারকে জনআকাঙ্ক্ষা পূরণ করতেই হবে। ব্যর্থ হতে দেওয়া যায় না। কারণ, এ সরকারের ব্যথর্তা হবে জনগণের ব্যর্থ হওয়ারই নামান্তর।
মুক্তিযোদ্ধা, সাংবাদিক ও গবেষক

