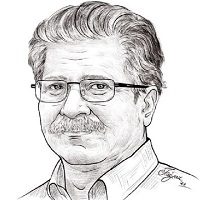-676fd70e38b70.png)
আবু সাঈদ খান
সুদূর অতীতে আমাদের সমাজে নানা মত ও পথের বর্ণিল সমাবেশ ঘটেছিল– যার প্রকাশ হতো কবিয়াল কবিয়ালের তর্কযুদ্ধে, বাউল-বয়াতির গানে ও মননে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। রাজা-সম্রাটরা গৌড়, দিল্লি বা মুর্শিদাবাদে বসে শাসন করতেন, তাদের সঙ্গে রায়ত-প্রজাদের সম্পর্ক ছিল খাজনা দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে মৌর্য-মোগল-পাঠানদের রাজদরবার এক রৈখিক ছিল না। সম্রাট অশোক ছিলেন পরমত সহিষ্ণু ও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানে বিশ্বাসী। নিজ নিজ মত চর্চার সুযোগ ছিল অবারিত। মোগল-পাঠানরা বহিরাগত হলেও তারা ভারতীয় শাসকে পরিণত হয়। সম্রাট আকবর তো বটেই, সব মোগল সম্রাটের দরবারে হিন্দুস্তানি রাজন্য-অমাত্যরা যথাযোগ্য মর্যাদায় আসীন হয়েছিলেন, এমন কী হিন্দুদের মধ্য থেকে সেনানায়কও নিযুক্ত হতেন। মান সিংহ ছিলেন সম্রাট আকবরের সেনাধ্যক্ষ। আকবরের রাজসভায় ঠাঁই পেয়েছিল ভারতীয় ধর্মশাস্ত্র, সংগীত, চিত্রকলা প্রভৃতি। একদিকে দারাশিকোর হাতে মহাভারত, গীতা, উপনিষদ ফার্সিতে অনূদিত হয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাতে ছড়িয়ে পড়েছিল। অপরদিকে বঙ্গের সুলতানদের পৃষ্ঠপোষকতায় রামায়ণ-মহাভারত বাংলায় অনূদিত হয়ে সাধারনণ মানুষের ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল।
আরব-ইরানি সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দুস্তানি সংস্কৃতির আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে সমন্বয়বাদী ধারা গড়ে উঠেছিল, ধর্মে ধর্মে ও মানুষে মানুষে নৈকট্য এসেছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেবকে নিয়ে অনেকে প্রশ্ন তোলেন। তিনি কট্টরপন্থি ছিলেন সত্য। তবে আকবর-শাহজাহানের আমলে সমাজ ও সংস্কৃতিতে যে সমন্বয়বাদী ধারা তৈরি হয়েছিল, আরঙ্গজেবের শাসনামলেও তা অব্যাহত ছিল। এ হলো ওপরের রাজনীতি। তৃণমূলে ছিল জননীতি। সমাজে নানা ধর্ম, মত ও পথের সহঅবস্থান ছিল। সনাতন, বৌদ্ধ, ইসলাম একই সমাজদেহে ঠাঁই পেয়েছিল। চার্বাক, বৌদ্ধ সহজিয়া, সুফি, বৈষ্ণব, বাউলরা মানবজমিনে শত ফুল ফুটিয়েছিল। ধর্ম-বর্ণে, জাত-পাতের বিরোধ কখনও কখনও জনজীবনকে অশান্ত করেনি তা বলা যাবে না। তবে সহঅবস্থান ছিল সর্বব্যাপ্ত। সমন্বয়ের ধারা ছিল বিকাশমান, যার প্রমাণ মিলে সাহিত্যেও। মধ্যযুগের কবি জয়ানন্দ হরিদাসের মুখে বলিয়েছেন–
শুন বাপ সবারই এক ঈশ্বর ।। নামমাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে। পরমার্থ এক কহে কোরানে পুরাণে।। ব্রিটিশ শাসনামলে সমন্বিত ধারার ছন্দপতন ঘটল। ইংরেজ শাসনের ‘ভাগ করো ও শাসন করো’ নীতি হিন্দু-মুসলমানের সমন্বিত সাংস্কৃতিক ধারায় ফাটল ধরিয়ে দেয়। একদিকে হিন্দু কলেজ, অপরদিকে আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পেছনে ছিল দুরভিসন্ধি। ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও বিভেদের বীজ বপন করা হয়। ব্রিটিশ ইতিহাসবিদগণ ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বকে ধর্মের ভিত্তিতে চিত্রিত করেন, মৌর্য, সেন, মোগল, পাঠান শাসন না বলে বৌদ্ধ, হিন্দু, মুসলিম শাসন বলে আখ্যায়িত করা হয়। তবে তাদের শাসনকে খ্রিষ্টান শাসন না বলে ব্রিটিশ শাসন উল্লেখ করা হয়।
ইংরেজ শাসক সুকৌশলে দুই প্রধান ধর্মাবলম্বী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে– যা প্রতিফলিত হয় রাজনীতিতেও। পরিণতিতে সাম্প্রদায়িক সংঘাত, রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা ও ১৯৪৭ সালের দেশভাগ। ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হলো। পূর্ব বাংলা হলো পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। দেশভাগের দুই দিন আগে অর্থাৎ ১৯৪৭ সালের ১১ আগস্ট মহম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তান গণপরিষদ অধিবেশনে সবাইকে চমকে দিলেন। তিনি স্পষ্ট করেই বললেন যে, ধর্ম-জাত-পাতভেদে রাষ্ট্র কোনো পক্ষপাত করবে না; সবাই হবে পাকিস্তানের সমমর্যাদার নাগরিক। ধর্মীয় জোশে জিন্নাহর ঘোষণা তলিয়ে যায়।
জিন্নাহর জীবদ্দশাতেই পাকিস্তান কট্টর ধর্মরাষ্ট্রে পরিণত হয়। কায়েম হয় ব্রিটিশ শাসনের আদলে কর্তৃত্ববাদী শাসন। অদ্ভুত যুক্তি হাজির করে শাসক মুসলিম লীগ। বলা হয়, আল্লাহ এক, কেতাব এক, রসুল এক। তাই পাকিস্তানে রাজনৈতিক দলও থাকবে একটি অর্থাৎ মুসলিম লীগ ছাড়া কোনো দল থাকবে না। মুসলিম লীগ নেতারা ফতোয়া দেন যে, মুসলিম লীগ পাকিস্তান কায়েম করেছে। তাই মুসলিম লীগের বিরোধিতা মানে পাকিস্তানের বিরোধিতা, আর পাকিস্তানের বিরোধিতা মানে ইসলামের বিরোধিতা। ১৯৪৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান ক্ষেপে গিয়ে বলেন, ‘যো আওয়ামী লীগ করেগা, উসকো শির হাম কুচাল দেগা।’ মুসলিম লীগের এই একরৈখিক রাজনীতিকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় পূর্ব বাংলার আপামর জনতা। বিগত শতকের চল্লিশ দশকের রাজনীতিতে হিন্দু-মুসলমান ছিল হানাহানিতে লিপ্ত।
১৯৪৭-উত্তরকালে মুসলিম লীগের স্বৈরশাসন মোকাবিলায় তারা হাতে হাত ধরে অগ্রসর হয়। রাজনৈতিক নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। অগ্রণী ছিল ঐক্যবদ্ধ ছাত্রসমাজ। ভাষা, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এক মোহনায় মিলিত হয়। সমাজদেহে যে অসাম্প্রদায়িক সমন্বয়বাদী ধারা বহমান ছিল, তা ক্রমেই বেগবান হয়ে রাজনীতিতেও অসাম্প্রদায়িক-ধর্মনিরপেক্ষ ও মানবিক ধারাকে পুষ্ট করে। গণতান্ত্রিক চেতনায় রাজনীতি শানিত হয়। তখন ছিল বিশ্বজোড়া সাম্যবাদী আন্দোলন। বাংলাদেশের রাজনীতি তার বাইরে ছিল না। রাজনীতিতে জাতীয়তাবাদ ও সমাজতান্ত্রিক ধারা একাকার হয়ে যায়। উনসত্তরে একই মিছিলে আওয়াজ ওঠে– জয় বাংলা ও জয় সর্বহারা; একটি আরেকটির বিরোধী ছিল না, ছিল পরিপূরক।
মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠিত হলো। পাকিস্তান ছিল মুসলমানের, আর বাংলাদেশ হলো হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সবার; বাঙালি, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরাসহ সব জনগোষ্ঠীর। সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হলো চার রাষ্ট্রীয় নীতি–গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাঙালি জাতীয়তাবাদ পাকিস্তানি আগ্রাসন রুখে দাঁড়িয়েছিল। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য, স্বাধীন বাংলাদেশে সেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ আগ্রাসী চরিত্র ধারণ করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের থাবায় জাতিগত সংখ্যালঘুরা বিপন্নবোধ করে।
১৯৭২ সালে গণপরিষদে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা এই আগ্রাসী নীতির তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি সংবিধানে সব জাতিসত্তার স্বীকৃতির দাবি জানান। একচেটিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠতার দাপটের কাছে তা শূন্যে মিলিয়ে যায়। সেদিন বাংলাদেশের নাগরিকদের বাঙালি বলে আখ্যায়িত হওয়ার প্রস্তাবের বিরোধিতা করে মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা বলেন, ‘আমি একজন চাকমা। আমার বাপদাদা, চৌদ্দ পুরুষ কেউ বলেন নাই, আমি বাঙালি। ...আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। আমরা আমাদের বাংলাদেশি বলে মনে করি এবং বিশ্বাস করি। কিন্তু বাঙালি বলে নয়।’
উগ্র বাঙালি জাতীয়তাবাদের থাবায় বহুত্ববাদ বিদীর্ণ হয়। রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কারণেই বাঙালি ও পাহাড়ি আদিবাসীদের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। পার্বত চট্টগ্রামে রক্তাক্ত হয়। অবশেষে ১৯৯৭ সালে সম্পাদিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির মধ্য দিয়ে রক্তপাতের অবসান ঘটে। পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নে গড়িমসিতে পাহাড়ি জনগোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অসন্তোষ ও নিরাপত্তাবোধের অভাব রয়েছে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মধ্যেও। আদিবাসী ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জানমাল ও উপাসনালয়ের ওপর একর পর এক দুর্বৃত্তের হামলা চলছে– তার প্রতিকারে রাষ্ট্রের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ। আশার কথা, বিলম্বে হলেও বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক পরিচয় বাংলাদেশি করা হয়েছে।
আদিবাসীদের লাগাতার আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে ২৩ ক অন্তর্ভুক্ত হয়। এতে বলা হয় যে, ‘রাষ্ট্র বিভিন্ন উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের অনন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও বিকাশের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।’ যদিও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠিসমূহের আদিবাসী হিসেবে স্বীকৃতির দাবি উপেক্ষিত। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা এখন প্রশ্নবিদ্ধ। ইসলাম এখন সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রধর্ম। ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলো ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে আপসরফা করছে। বিএনপি-জামায়াতঘেঁষা নীতি এবং আওয়ামী লীগ হেফাজত তোষণ নীতি নিয়েছে। এই আপসনীতির কারণে ধর্মভিত্তিক একরৈখিক সমাজের রাস্তা প্রসারিত হচ্ছে। সংগত কারণেই এটি সব ধর্মের, সব মানুষের শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের জন্য অশুভ সংকেত। বহুত্ববাদী সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য এখন বড় হুমকি কর্তৃত্ববাদ।
১৯৭২ সালের সংবিধান ছিল গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অনন্য দৃষ্টান্ত; যা ২য়, ৪র্থ, ৫মসহ একের পর এক সংশোধনীর কাঁচিতে ক্ষতবিক্ষত। গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বিত। একদা বাংলাদেশে নির্বাচন ছিল উৎসব, এখন তা ক্ষমতাবানদের হাতের মোয়া। রাষ্ট্র হয়ে উঠেছে আরও কর্তৃত্ববাদী। রাষ্ট্রের দাপট বাড়ছে, সেবা কমছে। চলছে দুর্বৃত্তের আগ্রাসন। লুট হচ্ছে ব্যাংক। দখল হচ্ছে জমি, নদী, খাল, বিল, ঝিল। এই দখলবাজিতে আমলা, পুলিশ, রাজনৈতিক কর্মীরা একাট্টা। রাজনীতির আশ্রিত দুর্বৃত্তরা চড়াও হচ্ছে নিরীহ ও দুর্বল মানুষের ওপর। ধর্মীয় ও নৃতাত্ত্বিক সংখ্যালঘুরা এই দুর্বৃত্তদের হামলার নির্মম শিকার। তাদের বাড়িঘর, দোকানপাট ও উপাসনালয়ে হামলা হচ্ছে। বাউল-বয়াতিরাও হচ্ছেন আক্রান্ত।
এক সময়ে রাজনৈতিক নেতাকর্মীরা সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হলে রুখে দাঁড়াত, তাদের বাড়িঘর পাহারা দিত। এখন তারা লুটপাটে নেতৃত্ব দিচ্ছে। পাহাড় ও সমতলের আদিবাসীদের ওপর হামলা হচ্ছে বাঙালির নামে, আর ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা হচ্ছে মুসলমান পরিচয়ে। এরফলে সংখ্যালঘুরা বিপন্নবোধ করছে। সেই সঙ্গে দূরত্ব বাড়ছে আদিবাসীদের সঙ্গে বাঙালির, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টানের সঙ্গে মুসলমানের। চূড়ান্ত বিচারে দূরত্বটা বাঙালি মুসলমানের সঙ্গে অন্য সবার।
এই সুযোগ নিচ্ছে সেই ধর্মান্ধ গোষ্ঠী, যারা একাত্তরের পরাজয়ের বদলা নিতে চাইছে। ধর্মান্ধ গোষ্ঠী কৌশলও বদলেছে, আশ্রয় নিচ্ছে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির মতো ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বী দলেও। উভয় দলের পক্ষপুটে তাদের ছানা-পোনা লালিতপালিত হচ্ছে। তারপরও বিশ্বাস করি, আমাদের বহুত্ববাদের চারণভূমিতে মৌলবাদ-জঙ্গিবাদের উত্থানের সুযোগ নেই। তবে তাদের শক্তি সঞ্চয় বহুত্ববাদী সমাজের জন্য হুমকি হয়ে উঠছে, আরও ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। বহুত্ববাদী সমাজ ও রাজনীতির জন্য যেমন গণতান্ত্রিক আবহ দরকার, তেমন দরকার পরমত সহিষ্ণু সংস্কৃতি। সেই ঐতিহ্য সুদূর অতীত ও নিকট অতীতে রয়েছে। সব ধর্মের, সব বর্ণের, সব মতের মানুষ এক কাফেলায় মিলতে পারে, তার অনন্য এক দৃষ্টান্ত মুক্তিযুদ্ধ।
হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়েছে, একই হাঁড়ির খাবার খেয়েছে। মানুষে মানুষে যে দূরত্ব ছিল– একাত্তরের রক্তস্রোতে তা ঘোচে যায়, সংস্কারের দেয়াল ধসে যায়। তাই, একাত্তরের ধ্বংসস্তূপের ওপর সেই সমাজ ছিল আরাধ্য–যেখানে ধর্ম থাকবে, ধর্মান্ধতা থাকবে না। হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, শিয়া, সুন্নি, আহমদিয়া থাকবে; কেউ কারও ধর্ম বা বিশ্বাসে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না; বাঙালি ও আদিবাসীরা থাকবে; কেউ কারও ওপর আধিপত্য বিস্তার করবে না। একাত্তরে আমরা সেই রাষ্ট্র চেয়েছি, যেখানে রাষ্ট্র সব ধর্ম, বর্ণ, মত ও পথের মানুষকে একই চোখে দেখবে। রাজনীতিতে মত-মতান্তর থাকবে, কিন্তু কেউ কাউকে নিধন করবে না। রাজনীতিকদের মধ্যে কবিয়ালদের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্কযুদ্ধ চলবে, কেউ কাউকে সংহার করবে না; এটিই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র তথা বহুত্ববাদী সমাজের মর্মবাণী।
লেখক মুক্তিযোদ্ধা গবেষক